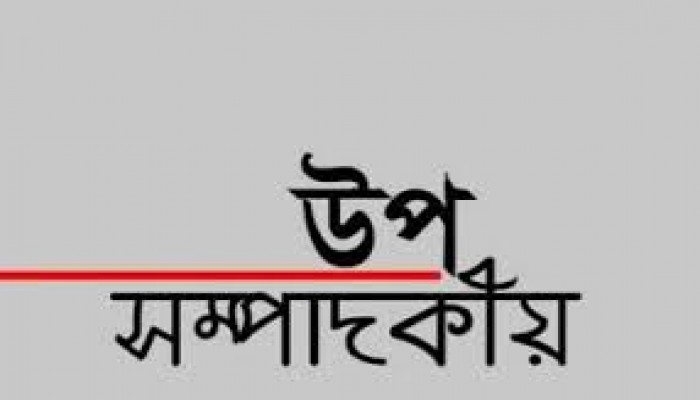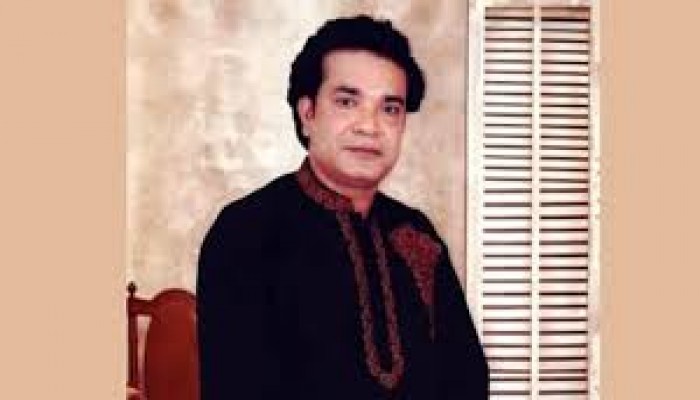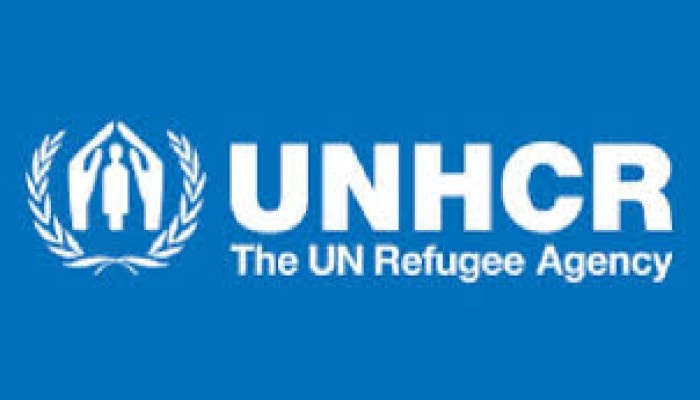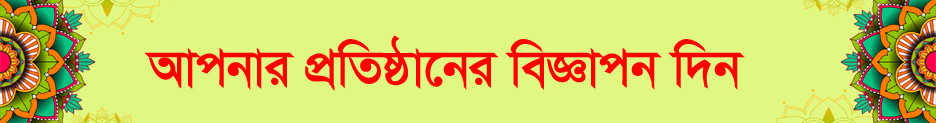
নির্বাচন পদ্ধতি ধ্বংস হলে লাভবান হবে চরমপন্থিরা

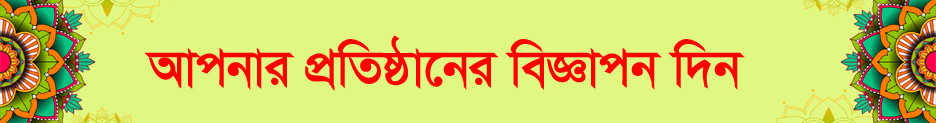
মোশাররফ হোসেন মুসা
বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলা শুরু করেছেন গণতন্ত্র হলো একটি সংস্কৃতি। সেজন্য গণতন্ত্র শুধু মুখে প্রচারের বিষয় নয়, অন্তরে ধারণের বিষয় এবং সর্বক্ষণ চর্চার বিষয়। জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে সেই চর্চায় অংশগ্রহণ করে। একটি গণতান্ত্রিক দলের প্রাণ হলো নির্বাচন। তবে যারা বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় যেতে চায় তারা নির্বাচন বিশ্বাস করে না। তাদের মধ্যে একটি হলো চরম বামপন্থি; অপরটি হলো চরম ডানপন্থি। চরম বামপন্থিরা ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হলেও চরম ডানপন্থিরা ধর্মকে আশ্রয় করে বেশ বাড়বাড়ন্ত। চরম বামপন্থিদের বক্তব্য হলো একটি দেশে শ্রমিক শ্রেণির মানসিকতাসম্পন্ন লোকের সংখ্যা কম থাকে। তাদের ভোটে কখনোই শ্রমিক দরদি নেতৃবৃন্দ নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে যেতে পারবে না। অপরদিকে চরম ডানপন্থিদের বক্তব্য হলো-একটি মুসলিমপ্রধান দেশে প্রকৃত ইমান-আকিদাসম্পন্ন লোকের সংখ্যা সীমিত থাকে। তাদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে একজন খাঁটি মুসলমান কখনোই পার্লামেন্টে যেতে পারবে না। সেজন্য বিপ্লব দরকার। বিপ্লবের পর বাছাইকৃত ব্যক্তিরা শাসনকার্য পরিচালনা করবে। সে কারণে আসন্ন মহাবিপদ থেকে দেশকে রক্ষার জন্য নির্বাচন পদ্ধতি বাঁচিয়ে রাখা জরুরি। সকলের জানা রয়েছে খ্রিষ্টপুর্ব আমলে গ্রিক নগর রাষ্ট্র থেকে গণতন্ত্রের সূচনা ঘটে।
তৎকালীন দার্শনিকেরা (প্লেটো ও অ্যারিস্টেটল প্রমুখ) গণতন্ত্রকে নিকৃষ্ট শাসনের মধ্যে উত্তম শাসন বলে বিবেচনা করতেন। মধ্যযুগে টমাস একুইনাস (১২২৫- ১২৭৪ খ্রি.) বলেছেন- যদিও রাজতন্ত্র একটি উত্তম সরকার; তবে সম্ভাব্য উত্তম সরকার হচ্ছে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের মিশ্র সরকার। তাঁর কথার কিছুটা রূপ দেখতে পাওয়া যায় মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ক্যানাডাসহ কিছুসংখ্যক ইউরোপিয়ান দেশসমূহে। টমাস হবস গণতন্ত্রের বিরোধিতা করে একনায়কতন্ত্রের পক্ষে বলেছেন। জন লক যে গণতন্ত্রের কথা বলেছেন, তা বর্তমানের পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের সঙ্গে মিল রয়েছে। ফরাসি দার্শনিক জ্যাক রুশো আদর্শ গণতন্ত্রের কথা বলেছেন। ইমানুয়েল কান্ট ব্যক্তির অধিকার এবং রাষ্ট্রের সীমিত ক্ষমতা রাখার কথা বলেছেন। জার্মান দার্শনিক হেগেল ব্যক্তি স্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতার কথা বলেছেন। কার্ল মার্কস শ্রেণিহীন সমাজের কথা বলেছেন। টকভেলি গণতন্ত্রকে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন বলেছেন। জন স্টুয়ার্ট মিল গণতন্ত্রের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। জন রউল সব নাগরিকের সমান অধিকারের দাবি করেছেন। অমর্ত্য সেন গণতন্ত্রের সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলেছেন। তবে যেসব দেশ সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়েছে সেসব দেশে গণতন্ত্র বিলম্বে এসেছে (সম্ভবত এ কারণেই দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা জেলখানায় থাকাকালীন এ সংকটটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি পুর্বেকার শ্বেতাঙ্গ শাসকদের সঙ্গে সমন্বয় করে সরকার পদ্ধতি চালু করেন)।
বৃটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করে স্বাধীনতা লাভ না করায় দেশটিতে নির্বাচন পদ্ধতি একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো লাভ করেছে। কিন্তু সর্বস্তরে গণতন্ত্রায়ন হয়নি। সুষম নিয়মে সকল রাজ্যে উন্নয়ন হচ্ছে না, জাতিভেদ-বর্ণভেদ দূর হয়নি, সর্বোপরি ধনী ও গরিবের বৈষম্য ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে ২০২৪ সালকে নির্বাচনের বছর বলা হচ্ছে। পৃথিবীর ৭০টি দেশে নির্বাচন হচ্ছে। প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী নির্বাচনে থাকছে। ভøাদিমির পুতিন বেশ কিছুদিন আগেই শপথ নিয়েছেন। যদি ভারতে নরেন্দ্র মোদি এবং যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প আবার নির্বাচিত হন, তাহলে ষোলোকলা পূর্ণ হয়।
এই অবস্থায় নির্বাচন নিয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিদের রম্যকথা পড়তে পারি; (১) জোসেফ স্টালিন বলেছেন- ‘যারা ভোট দেয় তারা কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় না। যারা ভোট গণনার দায়িত্বে থাকেন তারাই সিদ্ধান্ত নেন ফলাফল কী হবে? (২) জার্মান লেখক আমেরিঙ্গা বলেছেন- ‘রাজনীতি হচ্ছে খুব ভদ্রভাবে গরীবদের থেকে ভোট আর ধনীদের থেকে চাঁদা আদায়ের প্রক্রিয়া যাতে উভয় পক্ষকেই আশ্বাস দেওয়া হয় তারা উভয়পক্ষকে উভয়ের হাত থেকে রক্ষা করবে। (৩) ফ্রিল্যান্স লেখক জেরাল্ড এফ লিবারম্যান বলেন- ‘নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য যেখানে বলা হয় তারাও জনগণের অংশ। (৪) রম্য লেখক জেরাল্ড বারজান বলেন- ‘প্রতিটি নির্বাচন থেকে আমরা কী শিখি? আমরা এটাই শিখি যে আমরা আগের নির্বাচন থেকে কিছুই শিখিনি’। (৪) সাবেক সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট নিকিতা ক্রুশ্চেপ বলেন- ‘রাজনীতিবিদরা বিশ্বের সব জায়গায় একই রকম। তারা আপনাকে বিশাল সেতু বানিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেবে, হয়তো সেখানে কোনো নদীই নেই। (৫) মার্কিন সাংবাদিক এইচএল মেনকেন বলেন- ‘প্রতিটি নির্বাচন আসলে চোরাই মাল বিক্রি করার জন্য আয়োজিত উন্নতমানের নিলাম অনুষ্ঠান ছাড়া কিছুই নয়। (৬) সাবেক জার্মান চ্যান্সেলর বিসমার্ক বলেন- ‘মানুষ আর কখোনই এত মিথ্যা কথা বলে না যতটা তারা বলে থাকে কোনো (পশু) শিকার করার পর বা যুদ্ধের সময় অথবা নির্বাচনের সময়। (৭) ব্রিটেনের নির্বাক চলচ্চিত্র অভিনেতা ফ্রান্ক ডেন বলেন-’সবচেয়ে ভালো ব্যক্তিকে ভোট দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। তাকেই ভোট দিন যে সবচেয়ে কম ক্ষতিসাধন করবে। (৮) মার্কিন কলামিস্ট বিল ভন বলেন-আমেরিকার নাগরিকেরা অন্য দেশে গণতন্ত্র রপ্তানি করার জন্য প্রয়োজন হলে সাগর পেরিয়ে সে দেশে যুদ্ধ করবে; কিন্তু নিজের দেশে রাস্তা পার হয়ে ভোট দিতে যাবে না। ৯) মার্কিন কৌতুক অভিনেতা রবিন উইলিয়াম বলেন- ‘পলিটিক্স শব্দটির অর্থ পলি (ঢ়ড়ষর) হচ্ছে ল্যাটিন শব্দ, যারা অর্থ অনেক বা বহু। আর টিক্স (ঃরপং) হচ্ছে রক্ত চোষা পোকা। (১০) মার্কিন রহস্যোপন্যাস লেখক ডিন কুন্টজ বলেন- ‘কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করলো বর্তমান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দুজন প্রার্থী আছেন তাদের ব্যাপারে আপনার মতামত কী? উত্তরে বলেছেন, জীবনে যত হরর মুভি দেখেছি তার মাঝে সবচেয়ে ভয়াবহ দুটিকে বেছে নিতে বলা আর দুজন প্রার্থীর একজনকে বেছে নিতে বলা’। নির্বাচন ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যত কথাই বলা হোক না কেন, দিন শেষে আমাদেরকে গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলতে হয়। কারণ বর্তমান গতিশীল সমাজের যুগে এর চেয়ে উপযোগী মতাদর্শ দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া গণতন্ত্রের সুবিধা হলো এ মতাদর্শে অন্যান্য মতাদর্শ থেকে কল্যাণকর বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যেমন: বেকার ভাতা, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ইত্যাদি কল্যাণকর বিষয়গুলো সমাজতান্ত্রিক নীতি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে , আওয়ামী লীগ সরকার এবং বিরোধী দল বিএনপি ও তার মিত্র দলগুলো ক্ষমতায় থাকার জন্য ও ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তব্য দিলেও নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কারের পক্ষে কোনো রূপরেখা দিচ্ছে না। ধরা হয়, স্বাধীনতার পর ১৯৯১ সাল, ১৯৯৬ সাল, ২০০১ সাল ও ২০০৮ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। এটি রাজনীতিকদের জন্য বড়োই অবমাননাকর। কারণ নির্বাচনগুলো হয়েছে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দ্বারা।
বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা দুরূহ ব্যাপার ছিল। বারবার সরকার পদ্ধতি পরিবর্তন তার বড়ো প্রমাণ। তবে স্বাধীনতার ৫৩ বছর পর জবরদস্তিমূলক মানসিকতা এবং দলের পূর্বসূরিদের অন্ধ অনুসরণ মোটেই কাম্য নয়। কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা বর্তমানে ব্যক্তির শাসন নিয়ে এসেছে। এ ব্যবস্থা এখন তৃণমূল পর্যায়েও দৃশ্যমান হচ্ছে। সেজন্য একই সঙ্গে জাতীয় ও স্থানীয়তে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ডিজাইন গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশের আয়তন, ভৌগোলিক অবস্থান, ভূপ্রকৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য ইত্যাদি বিবেচনায় নিলে দুই প্রকারের সরকার ব্যবস্থাই বাস্তবায়নযোগ্য। তাহলো- কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা। কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য বৈশ্বিক ও জাতীয় কাজ নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। আর যাবতীয় স্থানীয় কাজ (গ্রামীণ ও নগরীয়) স্থানীয় সরকারের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। অব্যাহত নগরায়ণ এখন কঠিন বাস্তবতা। অপরিকল্পিত নগরায়ণের কারণে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেজন্য জলবায়ুর বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য পরিকল্পিত নগরায়ণ জরুরি। পরিবেশবান্ধব ও পরিকল্পিত নগরায়ণকে সামনে করে স্থানীয় সরকারের স্তর বিন্যাস করতে হবে। প্রতিটি স্থানীয় ইউনিটকে প্রজাতান্ত্রিক রূপ দিয়ে (তথা জেলা সরকার, নগর সরকার, ইউনিয়ন সরকার ইত্যাদি) স্থানীয় সরকারের কাজসমূহ এককভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর হবে ইউনিয়ন এবং নগরীয় স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর হবে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন উভয়ই। জেলা সরকার হবে গ্রামীণ ও নগরীয় স্থানীয় সরকারের সর্বোচ্চ স্তর। জেলা এক হাতে নগরীয় স্থানীয় সরকারগুলো ও অন্য হাতে গ্রামীণ স্থানীয় সরকারগুলো পরিচালনা করবে। কেন্দ্রের সাথে শুধু জেলার সম্পর্ক থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য ও স্থানীয় সরকারের জন্য পৃথক পৃথক কর্মকর্তা/কর্মচারী নিযুক্ত করার অথবা নিয়োগ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
প্রয়োজনে স্থানীয় সরকারের জন্য পৃথক ক্যাডার সার্ভিস চালু করতে হবে। সংক্ষেপে নগর সরকারের রূপরেখা বর্ণনা করা যেতে পারে। নগর প্রশাসন, নগর আদালত ও নগর সংসদ মিলে নগর সরকার প্রতিষ্ঠা হবে। নগর সংসদ নগরকেন্দ্রিক সকল সমস্যা চিহ্নিত করবে এবং নগর প্রশাসন সেটা বাস্তবায়ন করবে।
নগরে সংগঠিত সকল অপরাধের (নির্ধারিত) বিচার করবে নগর আদালত। এর বাইরে একজন নগর ন্যায়পাল থাকবেন।
তিনি মেয়র, কাউন্সিলর, নগর বিচারকসহ নগর সরকারের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ করবেন এবং যথাযথ ব্যবস্থা নিবেন। তাছাড়া নগর নির্বাচনি বোর্ড থাকবে। নগর নির্বাচনি বোর্ড এককভাবে নগর সরকারের নির্বাচন সস্পন্ন করবে। একই নিয়মে জেলা সরকার, উপজেলা সরকার (যদি প্রয়োজনীয়তা থাকে), জেলা সরকার গঠিত হবে। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সংসদে এবং স্থানীয় সরকারের সংসদ সমুহে ১০০: ১০০ প্রতিনিধিত্বে পুরুষ ও নারীদের নির্বাচিত করার ব্যবস্থা করতে হবে। লক্ষণীয়, শিক্ষক নির্বাচন, ছাত্র সংসদ নির্বাচন, শ্রমিক সংগঠনের নির্বাচন, প্রেসক্লাবের নির্বাচন, ব্যবসায়ী সমিতির নির্বাচন ইত্যাদি যদি স্ব-স্ব ব্যবস্থাপনায় হতে পারে তাহলে সামান্য ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন কেন স্থানীয় মানুষ করতে পারবে না! সেজন্য জাতীয় গণ্যমান্য ও গ্রহণযোগ্য রাজনীতিকদের নিয়ে জাতীয় নির্বাচনি বোর্ড এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে স্থানীয় নির্বাচনি বোর্ড গঠন করতে হবে। জাতীয় নির্বাচনি বোর্ড জাতীয় নির্বাচন এবং স্ব-স্ব স্থানীয় নির্বাচনি বোর্ড স্ব-স্ব স্থানীয় ইউনিটগুলোর নির্বাচন সম্পন্ন করবে। এ ব্যবস্থা গৃহীত হলে জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক মুল্যবোধ বৃদ্ধিসহ নাগরিকবোধ জাগ্রত হবে। সেই সঙ্গে গড়ে উঠবে আস্থার এক সমাজ।
লেখক : গণতন্ত্রায়ন ও গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার বিষয়ক গবেষক
কমেন্ট বক্স
সর্বশেষ সংবাদ